1-9
Prachin Bharate Shikkhay Dolit- Ek osomapto odhyoyon
Authors: Biplab Kumar Das

Number of views: 2557
শিক্ষা একটি সভ্য জনপদের উন্নয়ন পরিমাপের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। সমাজের মেরুদন্ড শিক্ষা, সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই সভ্যতার উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে প্রধানতম ভূমিকা পালন করে চলেছে। আক্ষরিক অর্থে ‘শিক্ষা’-র উৎপত্তি সংস্কৃত ‘শাস্’ ধাতু থেকে, যার অর্থ শাসন করা, শৃঙ্খলিত করা বা নিয়ন্ত্রিত ইত্যাদি। শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে যেমন সমাজের অতীত ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সময়ের পরম্পরা অনুযায়ী সঞ্চালিত হয় পরবর্তী অপত্য জনধারায় তেমনি বহিঃবিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তি মননের তথা সৃষ্টিশীলতার আদান-প্রদানও সম্ভব হয় শিক্ষার মাধ্যমে। ফলে ব্যক্তিকল্যাণ এবং সামগ্রিক অর্থে সমাজকল্যাণ তথা সামাজিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের সর্ব্বোত্তম উপায় হল শিক্ষা। আবার একথাও ঠিক যে, শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয় সংশ্লিষ্ট সমাজের সামাজিক দর্শন দ্বারা। ভারতবর্ষের এই সুপ্রাচীন সভ্যজনপদে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা যুগেযুগে সমৃদ্ধ হয়েছে বহু মনিষীর উন্নত জীবনদর্শন ও শিক্ষাভাবনা দ্বারা। প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আজকের সমসাময়িক শিক্ষাভাবনাতেও ভারতীয় সমাজদর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। মূলত সামাজিক চাহিদার নিরিখেই পরিচালিত হয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাপনা। ফলে শিক্ষাআঙিনায় বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপট, স্তরবিন্যাস, সামাজিক পরিবর্তন, গতিশীলতা, প্রথা-রীতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি ভারতীয় সমাজ লক্ষ্য করলে দেখা যায় বর্ণভেদ তথা জাতিভেদ ব্যবস্থা আমাদের সভ্যতার সবচেয়ে আলোচিত ভয়ানক তথা চিরপ্রাচীন একটি ক্ষত, যা যুগেযুগে শুধুমাত্র সমাজব্যবস্থাকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে নি, শিক্ষাব্যবস্থাও যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে এই অমানবিক অসাম্যের দ্বারা। যার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ শিক্ষায় আজও আমরা সঠিকমানের সমানাধিকার বাস্তবিক অর্থে প্রতিষ্ঠা করতে পারি নি। স্বাধীনোত্তর সময়ে আইন প্রনয়ণ, নীতি গ্রহণ, সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বা সংরক্ষণের মতো রাজনৈতিক মর্যাদাদান সবই হয়েছে নিম্নবর্ণীয় মানুষের সেবার্থে কিন্তু এই আশীর্বাদ সর্বজনীনতা বা সার্বিক সাফল্য লাভ করেনি সেভাবে। আজও সমাজের সেই ক্ষত নিরাময়ের আন্তরিক ও যথার্থ প্রচেষ্টার অভাবে শিক্ষাব্যবস্থাপনা বারবারে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে এই ঘৃণ্য সামাজিক কাঠামো বিন্যাসের দ্বারা। ফলে সঠিক মানের প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ হচ্ছে আজকের আধুনিক শিক্ষাচিন্তাও। যদিও এই ব্যর্থতার কারণসমূহ বয়ে এসেছে কালের বহমানতায়। প্রাচীন বর্ণভেদ প্রথা কালক্রমে সংকীর্ণ ব্যক্তি-স্বার্থ বা অন্যান্য সামাজিক কারণে আজকের জাতিভেদে রূপ বদলেছে । ফলে এই অসাম্যেরও গঠনগত পরিবর্তন এসেছে সময়ের সাপেক্ষে, যা প্রতিটি যুগের শিক্ষা উদ্দেশ্যকে ব্যহত করেছে বিভিন্নভাবে। সভ্যতার উষালগ্নে প্রাচীন যুগের বৈদিক শিক্ষায় সর্বপ্রথম এই অসমসুযোগের ধারা পরিলক্ষিত হয়, যা পরবর্তীতে মহাকাব্যের যুগ ধরে মধ্যযুগে এমনকি আধুনিক যুগেও বিভিন্ন রূপে ও মাত্রায় প্রকাশিত। বর্ণভেদের মতো অসামাজিক প্রথার উপস্থিতির কারণেই প্রাচীনবৈদিক কালের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন অসাম্যের রূপ আমরা দেখতে পাই, যা সমসাময়িক কালেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। যদিও এর ব্যাতিক্রমী দর্শনও ছিল। প্রাচীন কালের ভারতীয় শিক্ষায় একমাত্র বৌদ্ধভাবনাতেই সামাজিক সাম্যের ও শিক্ষায় সমানাধিকারের সুর ধ্বনিত হয়েছিল। আবার বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করেও মহাকাব্য যুগের শিক্ষা হয়ে উঠেছিল অনেকটাই বাস্তব ও বৃত্তিভিত্তিক। অর্থাৎ প্রাচীনকালের ভারতীয় শিক্ষায় শূদ্রের অবস্থান বিভিন্ন সময়ে ভিন্নভিন্ন আঙ্গিকে পরিলক্ষিত ও আলোচিত হয়েছে দৃঢ়তার সঙ্গেই। এই লেখায় প্রাচীনকালের ভারতীয় শিক্ষায় বর্ণভেদের উপস্থিতি বা শিক্ষায় শূদ্রের অবস্থান তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। বৈদিকযুগের বিভিন্ন সময়ের সামাজিক বিন্যাসকরণের আলোকে সেযুগের শিক্ষাব্যবস্থাপনার অসম দিকটি আলোচিত হয়েছে প্রত্যক্ষভাবেই। প্রকৃত অর্থে এটি একটি অসমাপ্ত অধ্যয়ন ……
 Today
Today Yesterday
Yesterday This week
This week Last week
Last week This month
This month Last month
Last month All days
All days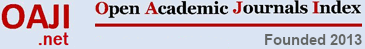


 Number of views: 2557
Number of views: 2557